অবক্ষয়, সংকট, সংশয় ও উচাটন মন। এই বিবিধ অভিব্যক্তি এবং এই
অভিব্যক্তিসমূহ স্বতন্ত্র আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিসর দাবি করে। চেতনায় আসে প্রত্যয় আকারে বটে; কিন্তু মননে, চিন্তায় অপ্রতিরোধ্য আলোড়ন তোলে।
তার স্বরূপ চেতনাতে চায়; পরিস্থিতি, পরিপ্রেক্ষিত, স্থান, কাল ও পাত্রের সাপেক্ষে প্রত্যয়সমূহের বোধগত স্বরূপ ধৃত হতে থাকে; উন্মোচিত হতে থাকে অবক্ষয়ের পরিধি, সংকটের স্বরূপ, সংশয়ের কার্যকারণ ও উচাটন মনের উদ্বেগাকুল অভিব্যাক্তি। মামুলি জিজ্ঞাসা এমনও হতে পারে, কেমন অবক্ষয়, কোথায় সংকট, কিসের সংশয়? প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসাসমূহ উস্কে দেয় আর জিজ্ঞাসাসমূহ প্রসঙ্গের অন্তরবাহির বিশ্লেষিত করে চলে উত্তরানুসন্ধানে আর সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন পথের খোঁজে।
অবক্ষয় সমাজ-রাষ্ট্রের, সংস্কৃতি ও মানুষের। ফলে প্রসঙ্গটি সামগ্রিকতার ও সামষ্টিকতার। তখন একক ব্যক্তির উদ্বেগ আর
তার একার থাকে না, হয়ে ওঠে সাধারণ ও সাধারণের। একক ব্যক্তি আহমদ ছফার সেই উচাটন মনের উদ্বেগসমূহ সাধারণের কিংবা সবার এবং এটিই আলোচনার প্রকৃত পরিধি।
অবক্ষয় নিয়ে তো
নানান কথা আর
নানান জনের কথা আছে; থাকে আর
ছিলোও। নতুন ব্যাপার নয় মোটেও। একে কতোভাবেই যে দেখার সুযোগ রয়েছে! Ôঅবক্ষয়: সামাজিক পরিবর্তনশীলতার একটি রাজনৈতিক পরিভাষা’ এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে অবক্ষয় বিষয়টিকে নানাবিধ জিজ্ঞাসা, সংশয়, প্রচলিত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের সাপেক্ষিকতায় বুঝতে ও
আপ্ত বোধটিকে জ্ঞাপনযোগ্য করে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম একবার। সেটি সম্ভবত ২০১৫ সালের ঘটনা। Ôউতঙ্ক’ নামের একটি সাহিত্য পত্রিকার Ôঅবক্ষয়’ সংখ্যায় তার স্থান হয়েছিলো। আর এই মুহূর্তে এসে বাংলাদেশের প্রথিতজশা চিন্তাবিদ, সাহিত্যমতি আহমদ ছফার অবক্ষয় সংক্রান্ত শঙ্কার সাথে আমি পুনঃ সমাত্ম ও সমাহিত হতে তাড়না বোধ করেছি।
তাঁর শঙ্কার নানান পরিপ্রেক্ষিত। তাঁর ভাবনার প্ররিপ্রেক্ষিত এবং সাপেক্ষিক-বিষয়-পরিধি সচেতন মানুষের আরো নানান ভাবনা ও দুর্ভাবনা বিস্তার করে চলে।
বিষয়টি নিয়ে সচেতনরূপেই বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট উচাটন ছিলেন সমাজমতি ছফা। তাঁর বিভিন্ন লেখায় সউদ্বেগে তা প্রকাশও করেছেন। তাঁর সৎ লেখক সত্তা, সচেতন মন-মনন ও
স্বদেশ-সংস্কৃতির প্রতি যথার্থ মমত্ববোধ তাঁকে উচাটন করে রেখেছিলো। আজ থেকে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বে তাঁর একটি লেখায় তিনি অবক্ষয়ের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছিলেন।
সে লেখাটির শিরোনাম ছিলো Ôঅবক্ষয়ের সংজ্ঞা’। তাঁর পূর্বকৃত ভাবনায় আর আমার বর্তমানের বোধে বিষয়গত অন্বয় তাঁর প্রতি বিনত রাখ আমাকে।
যদিও এই অন্বয় সত্ত্বেও কিছু সমালোচনার অবকাশ থেকেই যায়।
‘আমার কথা ও
অন্যান্য প্রবন্ধ’ লেখকের প্রকাশিত, অপ্রকাশি অগ্রন্থিত লেখাসমূহের একটি সংকলন।
ফলে, তাঁর প্রয়াণপরবর্তী কালে লেখাটি গ্রন্থিত বলে নিঃসংশয় হওয়া যায় না যে, এই লেখাটির শিরোনাম তিনিই নির্ধারণ করেছিলেন। লেখাটির শিরোনাম যদিও Ôঅবক্ষয়ের সংজ্ঞা’, তবু লেখাটির কোথাও অবক্ষয় ধারণাটির সংজ্ঞায়নের চেষ্টা লক্ষিত হয় না। বরং সমাজের অবক্ষয় সূচক বেশ কিছু ঘটনা ও পরিস্থিতি নমুনাস্মারক হিসেবে তিনি সেখানে উপস্থাপন করেছেন। তা থেকে অবক্ষয় বিষয়টিকে ছফার দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় বটে, কিন্তু, সমাজের অন্য আরো সচেতন কিংবা অচেতন মানুষেরও এই সকল ব্যাপারে একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, আর রয়েছেও এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সেই প্রলক্ষণসমূহ Ôঅবক্ষয়’ সূচক বিবেচিত হবে কিনা সে বিষয়ে ছফা মনোদৃষ্টি দেন নি। তিনি যেমন বোধ করেছেন তেমনটি আর সকলে মনে নাও হতে পারে।
তাদের এতদবিষয়ে ভিন্ন কিংবা বিপরীত মত থাকতেই পারে এবং এই প্রসঙ্গটি একটি মীমাংসাহীন বির্তকের জন্ম দিতে পারে। সুতরাং এই
বিতর্ক এড়িয়েই আলোচনার অগ্রগমন যথার্থ হবে, বোধহয়। বির্তক এড়াতে চাই, কিন্তু প্রসঙ্গান্তর কিছুতেই করতে চাই না। আগেই বলেছি, অবক্ষয় ব্যাপারটি সামাজিক পরিবর্তনশীলতার একটি প্রলক্ষণ এবং এবিষয়ক আলোচনাটি অবশ্যই রাজনৈতিক এবং তা ব্যক্তিক ও সামষ্টিক মূল্যযুক্ত, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও মূল্যবোধ সাপেক্ষও। যেহেতু তা
রাজনৈতিক, ফলে অবশ্যই একটি সমাজ-রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতেই এর আলোচনা অনিবার্য এবং সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনাও এর
সাথে অবশ্য প্রাসঙ্গিক।
ছফা উচাটন ছিলেন সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, মানুষ ও মানুঝের জীবন নিয়ে; জীবন ধারণের পন্থা নিয়ে। জীবন ধারণের পন্থা; এবং ফের সংস্কৃতির প্রসঙ্গ। উদ্বেগের বিষয় বাংলাদেশের মানুষের জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি। প্রসঙ্গ শিরোনাম ‘বাংলাদেশ: দেশ ও
জাতি’। প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম জিজ্ঞাসা, ‘বাংলাদেশের কি কোনও ভবিষ্যৎ আছে? সেই জ্ঞাসাটি প্রথমেই আমাদের যত্নে আড়াল করা হতাশাবোধে মৃদু কম্পন তোলে এবং তা
তরঙ্গায়িত প্রবাহে সমগ্র মর্মে ছড়িয়ে পড়ে।
হতাশায় নিমজ্জিত হই আমরা। পুনঃ প্রশ্ন হয়তো করেই ফেলি, আদোও কি বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ আছে? অথর্ব, ভীরু চিন্তকগণ জিজ্ঞাসার মুখেই মুষড়ে পড়েন। কিন্তু, প্রসঙ্গ পরিপ্রেক্ষিতে ছফার অবস্থানটি প্রণিধানযোগ্য ও ভীষণ আশার। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ, এর সম্ভাবনা ও ভবিষ্যতের বিষয়ে ছফাকৃত নিশ্চিন্তির আশ্বাসটি তাঁর যুক্তির নিরিখে খুবই প্রাসঙ্গিক তখন, যখন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়-বাস্তবতা দাঁত খিচিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসতে রত। ফলে তাঁর দূর্ভবনা মূর্ত হয়
তার জিজ্ঞাসার মধ্যেই এবং আশ্বাসের একটি স্থান যদিও থাকে, তবু, সংশয়মুক্ত হওয়া সহজ নয়। সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্ক্সের Ôঅর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ’ নামে একটি তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্বের সাথে কিছু ক্ষেত্রে কিছুমাত্রায় বিমত প্রকাশ করার যুক্তি ও
কার্যকারণ সিদ্ধ অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একটি ভূখণ্ডাশ্রিত জনমানুষের জাতি হিসেবে ও সে ভূখণ্ডটির জাতি-রাষ্ট্ররূপে পূর্ণতর বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত Ôসাংস্তৃতিক উন্নয়ন’ তা যে অর্থনৈতিক কাঠামো ও
ক্রিয়াকৌশলের উপরে নির্ভশীল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ এখানে মানতেই হয়। হ্যাঁ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উদ্বেগের কারণ। ছফা যখন এবিষয়ে উদ্বেগাকুল তখন বাংলাদেশের জনসংখ্যার ষাটভাগ মানুষ ভূমিহীন। তারা কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন আর তাদের জন্য শিল্পোৎপাদনে যুক্ত হবার কোনো সুযোগ একেবারেই নেই। ভবিষ্যতে মাথাতুলে দাঁড়ানোর পরিসরে বাংলাদেশের মাথার উপরে এই
বোঝাটি মস্তবড়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের অব্যবহতি পরেই, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ-বাস্তবতা কি বাংলাদেশের মানুষের কোনো ভাবিষ্যতের রূপরেখার আভাস সম্ভাবিত করতে পেরেছিলো, নাকি অতল আঁধার-সমুদ্রকেই প্রকট করেছিলো? এই জিজ্ঞাসা এবং সম্ভাব্য উত্তরসমূহ অবধারিতভাবেই আমাদেরকে হতাশার মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু, ছফা আশা দেখান, আমাদেরকে হতাশার গভীরখাতের কিনার থেকে সরিয়ে আনেন এবং অবশ্যম্ভাবী পতনের ভীতি থেকে রক্ষা করেন।
আমরা তার দেখানো আলোকটুকুকে আর মায়া কিংবা আলেয়া ভাবতে পারি না। ছফা বাঙালি চরিত্রের সঠিক বৈশিষ্ট্যটিই আমাদের চিনিয়ে দেন, আর তা হলো বাঙালির সংগ্রাম-সাধনা। বাঙালির ইতিহাসের গৌরবান্বিত পরম্পরায় দেখা যায় যে, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থাটি বিশেষ আশাব্যঞ্জক ছিলো না কখনোই, কিন্তু বাঙালির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়
নি; বাঙালি হারিয়ে যায নি তাই বলে। ফলে বাঙালিদের টিকে থাকার তাড়নাতেই টিকে থাকতে হয়, টিকে থাকে আর টিকে থাকবেও।
আশার এই সূত্রটি জাতির ভবিষ্যতের জিজ্ঞাসায় অমোঘ ইঙ্গিত হয়ে থাকে। অতীতের বহুবর্ষ ধরে নিপীড়িত হতে হতে, মার খেতে খেতে টিকে থাকার মধ্যেই বাঙালির আর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আছে।
এই সম্ভাবনাকে ছফা অনেক বড় করেই দেখেন।
বাঙালির আত্মার গহীনে কোথাও তিনি একটি ফিনিক্স পাখিকে দেখেন।
তবু, এবং তবু, তাঁর সংশয়ও যুগপৎ জাগ্রত। এই সংশয়ের মুখে আশাজাগানিয়া অতীতের গৌরান্বিত উদাহরণসমূহকেও আর ভবিষ্যতের উদ্গমসম্ভাবী বীজ ভাবা সহজ হয় না। অতীত গৌরব কিংবা সম্ভাবনার বীজটি বর্তমানের বন্ধা, শুষ্ক মাটিতে শুকিয়ে যেতে থাকে; আর কেবল অতীতই পড়ে থাকে সম্মুখে।
তবু, চরম অধঃপতনের মধ্যেও ভবিষ্যতের একটি প্রতিশ্রæতি অবশ্যই থাকে, নিশ্চয়ই থাকে। এই আশাবাদ ছফারই।
সমাজ, রাষ্ট্রের অবস্থা যতো খারাপই হোক না
কেন, সেখানে ভবিষ্যতের একটি প্রতিশ্রæতি থাকেই। ছফা দেশের মেধাবী সন্তানদের চিন্তাসম্পদের ওপরে ভরসা করতে চান। উত্তরণের কিছু সম্ভাবনা সেখানে নিশ্চয় আছে। Ôনানা জ্ঞান-বিদ্যার মানদণ্ড প্রয়োগ করে এই প্রতিশ্রতিটিকে দিবালোকে টেনে আনাই হল জ্ঞান এবং বিদ্যার ভূমিকা।’ এটিই একটি দেশের চিন্তকমহল, পণ্ডিৎকুল বা বুদ্ধিজীবি শ্রেণির কাজ।
এটি তাঁর ভীষণ আশাবাদের ভূমি। তবু, এইটিই যখন আশাবাদের জায়গা, তখন সংকটটিও এখানেই। কারণ, দেশের যে
সকল পণ্ডিৎদের বিদ্যাচর্চায় সংকট থেকে উত্তরণের আলোকসম্ভাবী দ্বার, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রæতিটি বেরিয়ে আসবে, সেই চিন্তকগণ যখন কেবল ভবিষ্যতের সংশয় ও আশঙ্কা প্রকাশ করেই খান্ত ও হতাশায় মুষড়ে পড়েন তখন সত্যিই আর
আশা থাকে না। এইটিই অবক্ষয়।
এবং এবিষয়ে আমার কিংবা আমাদের আর
সংশয় থাকে না। অবক্ষয় সংস্কৃতিগত, নিশ্চয়ই। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় মানে সমাজের সর্বাঙ্গজুড়েই পচনের চিহ্ন, ক্রমশ ক্ষয়রেখা। তিনি সমাজের নানান অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ অবক্ষয়ের প্রলক্ষণসমূহ চিহ্নিত করেছেন।
অবক্ষয় দেশের মানুষের আদর্শগত, রাজনৈতিক প্রতিশ্রæতিগত ও
ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার স্থানে, সর্বোপরি সাংস্কৃতিক মানে। বাংলাদেশের মানুষের অবক্ষয় নৈতিকতাহীনতা, ধর্মের বিপণন, মূল্যবোধের ক্রমশ স্খলন ও চরিত্রে পাশবিকতা ভরকরাসহ নানান প্রলক্ষণে প্রকটিত। এইসমূহ অবক্ষয় তাঁর নিবিড় অবলৌকনে ধরা দিয়েছে আর
তাঁর সমাজসচেতন মানস হয়েছে উচাটন।
দেশের ভবিষ্যৎ, বিকাশ ও উন্নয়নের স্বপ্নটির বাণিজ্যিকীকরণ একটি ঘৃণ্যতম সংকট। এই বাণিজ্য ও স্বার্থান্বেষার কারণে নানান সামাজিক সূচকে অবক্ষয়মাণ পরিস্থিতি প্রকটিত হয়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ নিশ্চয় নেতিবাচক কিছু নয়, কিন্তু, এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যখন সাংস্কৃতিক দেওলিয়াত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখন এই প্রক্রিয়াটিতে Ôসিঁদুরে মেঘে আগুনের ভীতি’ আছে। তেমনই একটি ব্যাপার হলো পাশ্চাত্যমূল্যবোধের আমদানি ও
তা নিয়ে ব্যবসা খুলে বসা। পাশ্চাত্য মূল্যবোধে নেতিবাচকতা দেখছি না,
বরং সেখানে উদারনৈতিকতার বিস্তৃত পরিসর রয়েছে।
বলছি ব্যবসায়ের কথা, Ôএনজিও’ ব্যবসায়ের কথা। এই ব্যবসায় ছফাকে উচাটন করেছে আর Ôইংরিজি-ইংরিজি আন্দোলন’ এই লেখটি তাঁকে লিখতে হয়েছে, তার উদ্বেগাশ্রিত ক্রোধাভিব্যক্তি জানাতে হয়েছে।
নারীমুক্তির আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলনÑ সমাজের এই
ইতিবাচক পরিবর্তন প্রক্রিয়াটিকেও কটাক্ষ করতে হয়েছে ব্যবসাজাত নোঙরামির কারণে। এটি নিঃসন্দেহ কথা যে
নারীমুক্তির আন্দোলনে যতো সভা-সেমিনার, র্যালি ও প্রচার প্রচারণা চলেছে ও তাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তা যদি নারীর অবস্থান উন্নয়নে ব্যয় করা যেতো তবে এদেশের নারীগণ প্রকৃতই কিছুটা অগ্রসর হতে পারতো, এটা নিঃসংশয়ে বলা চলে।
কিন্তু, দেখা যায় নারীমুক্তির ব্যানারে বৈদেশ থেকে যতো অর্থ আসে তার সিংহভাগ এই
এনজিওসমূহের আত্মসাতেই হাওয়া হয়ে যায়। ঠিক অনুরূপ ব্যাপারই ঘটে দারিদ্র্যবিমোচন ক্যাম্পেইনে। এনজিও ব্যবসায়ীদের প্রভূত আর্থিক উন্নয়ন ঘটে, তারা ফুলে-ফেঁপে ওঠে; কিন্তু, তাতে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দরিদ্র্যাবস্থার কোনো স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন হয় বা হয়েছে এমন কথা দাবী করা যায় না। এমন নানান অসংগতিই দেশ ও জাতির সংকট ও
সংশয়কে জিইয়ে রাখে।
চারপাশের অসংগতিসমূহ দেখে ছফা উচাটন মন নিয়ে চোখ খুলে রাখেন, চৈতন্যে অতন্দ্র ও সজাগ সমাজযাপন চলতে থাকে তাঁর।
তিনি বাংলাদেশকে নানামুখী দৃষ্টিকোণে অবলৌকন করতে থাকেন। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষণসমূহ আমাদের জানাতে থাকেন তার নানা শিরোনামের লেখায়। তাঁর লেখার একটি শিরোনাম কিছুতেই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না এবং এড়ানো একেবারেই অনুচিতÑ‘আমি বাংলাদেশকে যেভাবে দেখি’Ñঅর্থাৎ তিনি বাংলাদেশকে যেভাবে দেখেছেন। বাংলাদেশকে দেখার তাঁর নির্মোহ চোখ ছিলো।
বাংলাদেশের অতীত, ভূত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর সংশয় মিশ্রিত সচেতনতা সব সময়েই ছিলো। উল্লিখিত শিরোনাম প্রবন্ধে তিনি সেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর সে সংশয়কে আমরা অমূলকও ভাবতে পারি না। অমূলক ভাবতে পারি না বলেই এই সংশয় আমাদের অস্তিত্বমূল কাঁপিয়ে দেয়। সংশয় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন নিয়ে ও এদেশের মানুষের জাতিত্বসূচক আত্মপরিচয় নিয়ে। এই সংশয় ও
বির্তকের গর্ভভূমি ভারতবর্ষের বহু বছরের ইতিহাস ও বাংলাদেশের জন্মসূত্র। এমনকি বাংলাদেশের জন্মপূর্ব ও পরের অনেক সংশয় ও জিজ্ঞাসা এবং জবাবের উৎসও রয়েছে সেখানে।
নানান সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংঘাত পেরিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে, নবপ্রাণে, নতুন পরিচয় নিয়ে অগ্রযাত্রার প্রত্যয়ে। বাংলাদেশ একটি স্বপ্নকে সামনে রেখে এগুতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু, সংকটসূচক জিজ্ঞাসাটি হলোÑ তার স্বপ্নটি কী? মানুষের মনে এই
প্রশ্নটির উদয় হয়
বাংলাদেশের জন্মের অব্যবহতি পরেই এবং এই
জিজ্ঞাসার কোনো নিঃসংশয় উত্তর পাওয়া যায় নি, যায় না। ফলে এর
যাত্রাপথের দিশা অস্পষ্ট, গন্তব্য অনির্দেশিত। এবং এটি কেবল আহমদ ছফারই সচেতনতার অংশ, তা নয়; বরং স্বদেশপ্রেমী, ইতিহাস সচেতন সকল বাংলাদেশের নাগরিকেরই এটি সংশয়, দ্বিধা ও
দিকনির্দেশহীনতা প্রসূত একটি জিজ্ঞাসা। বাংলাদেশ একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমুখে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। কিন্তু, বাংলাদেশের মানুষের জাতিত্বের ভিত্তিটি কী হবে, যেখানে ধর্মীয় সম্প্রদায় চেতনাভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান ভেঙে তার জন্ম? তখন দ্বিধাশ্রিত নতুন প্রশ্ন এই যে, বাংলাদেশের জন্ম কি
তবে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্বকে অসফল প্রমাণ করেছে? তৎকালে অনেক চিন্তকই এই প্রশ্নের মুখে ‘হ্যাঁ’ সূচক জবাব দেন। এবং এই
ইতিবাচক মানস ফানুসে ভর করে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু। ধর্মীয় সম্প্রদায়চেতনাকে পরাস্ত করে ভাষা-সাংস্কৃতিকচেতনা ভিত্তিক জাতিত্বের ধারণাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার খুব অল্পকাল পরেই ফানুসরূপেই প্রমাণিত হয়েছে। ফলে জাতিগত পরিচয়ের প্রশ্ন, স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতির চরিত্র ও বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মননÑএই
সবকিছুই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে একটি প্রশ্নের জন্ম দেয় আর ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে।
প্রশ্নটি এইÑবাংলাদেশ কোথায় পৌঁছাতে চায়? সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও
রাজনৈতিক বিবেচনাতেও তা কুয়াশাচ্ছন্নই। এই কুয়াশাচ্ছন্নতা যেন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টাদের চেতনাদৃষ্টিতেই। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তির একটি অনিবার্য তাড়না এ অঞ্চলের মানুষ অনুভব করেছিলো নিঃসন্দেহে, কিন্তু, পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়েই সেটি হতে হবে এমন দাবী তখনও কোনো স্বপ্নদ্রষ্টা করেন নি। ছয় দফা দাবী তো
সেই স্বাক্ষ্যই দেয়। ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যের দাবীটিও প্রকটিত হয় নি ছয়দফাতে, ভাষাভিত্তিক জাতিত্বের দাবী তো
অনেক দূরের কথা।
কিন্তু, ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত একটি অন্তঃস্রোতা প্রবাহ ছিলো।
এই স্রোত বাঁধ ভেঙেছিলো পাকিস্তানি শাসকের গোয়ার্তুমির কারণেই। অত্যাচারিতের অনড় অবস্থান তাদের ভাঙনকে ত্বরাণিত করেছে, অনিবার্য করে তুলেছে।
যদিও, অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক অস্তিত্বের পেছনে তার স্বভাষার জন্য সংগ্রাম একটি মহান-ব্যাপার।
এটি বিশ^ পরিসরেই অনন্য রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত। কিন্তু, ১৯৭১ সালের পূর্বেই যে
এদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের মনে ও
মননে ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রের প্রকল্পনা দানা বেঁধেছিলো, এই দাবি বাজি ধরে করা যায় না। কিন্তু, স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ ও ভারতের অনেকেই একথা বলতে শুরু করেন যে, ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্মটি সেই দ্বিজাতিতত্ত্বকেই ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে এবং এদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দও তা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন; আর তদ্রƒপেই প্রচার-প্রচারনা চালাতে থাকেন।
তবে, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তা পুরো অভ্রান্ত ছিলো না
মোটেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এ অঞ্চলের বিপুলসংখ্যক মানুষই ধর্মের প্রশ্নে পাকিস্তান ভাঙার বিরোধী ছিলো। এটি তিক্তবাস্তবতা বটে, কিন্তু স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনীতি যেভাবে মোড় নেয়, দেখা যায় বাংলাদেশের মানুষের মনে ধর্মের প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে আর একাধিক রাজনৈতিক দল এটিকে পুঁজি করে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভে ভীষণরূপে ক্রিয়াশীল। এবং এর
পরেও ১৯৭৫ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সকলেরই জানা।
২০১৮ সালেও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জনে ধর্মের সমর্থন ও অবলম্বনই অনিবার্য হয়ে উঠেছে এবং যে রাজনৈতিক দলটি ১৯৭১ সালে ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস
করতো, তাদের রাজনীতিতেও এইসময়ে ধর্মই প্রধান হয়ে উঠেছে। ফলে, ভাষাভিত্তিক জাতিত্বের দাবীটি আর
প্রশ্নাতীত থাকে নি। পূর্বেই বলেছি, তা ফানসরূপেই প্রতিপন্ন হয়েছে, কেন না, তা ধর্মের কাঠির খোঁচায় ফুটো হয়ে চুপসে গেছে। প্রকৃতই, উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরবর্তীকালে দ্বিধা তৈরি করেছে আর তা সংকটকালেরও স্বাক্ষর। ছফা সংকটটি বুঝেছিলেন আর চিহ্নিত করেছিলেন যথার্থ।
ছফার উদ্বেগের নানান পরিক্ষেত্র। তাঁর লেখাতে স্বদেশ চেতনা ও আত্মসংস্কৃতি চেতনার আলোচনা-সমালোচনা ঘুরেফিরেই এসেছে। এবং রূপান্তরশীল এই বিয়ষগুলো নিয়ে সর্বদাই সজাগ থেকেছেন। তিনি দেখেছেন স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে কী
পরিমাণ ব্যক্তিস্বার্থ লিপ্সা ও
দলীয় স্বার্থ প্রধান।
সেখানে দেশের সার্বিক মানুষের স্বার্থ ও
মঙ্গলপ্রয়াশের চিন্তাটি ভূলুণ্ঠিত। স্বদেশ চেতনা, জাতিগত অহংকার আর
ধর্মনিরপেক্ষ, উদারনৈতিক সমাজ-সংস্কৃতি ও শোষণ মুক্ত অর্থনীতিভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের প্রসঙ্গটিই বাতুলতা। ছফা যেন সেই বাতুলদেরই একজন। অবক্ষয়, অসততা ও
খেয়োখেয়ীর বিপরীতে তাঁর সোচ্চার লেখনী। তাঁর চিন্তাশীল অজস্র লেখার মধ্যে থেকে একটি সংকলন Ôআমার কথা ও
অন্যান্য প্রবন্ধ’ থেকে আরো কিছু লেখার শিরোনাম এখানে উল্লেখ্যÑ‘এবারের কবিতা উৎসবে যা ঘটেছিল’, ÔভাবুকমÐলী, আনন্দগোষ্ঠী এবং আরো কিছু প্রসঙ্গ’, Ôপ্রসঙ্গ বাঙালি মুসলমান’, Ôযযাতির গল্প’, ‘আনন্দবাজার উপাখ্যান’, Ôপশ্চিমবাংলার বই বাংলাদেশে কাদের স্বার্থে’, Ôকোলকাতা বইমেলা: একটি বিশ্লেষণ’, ‘মিলেনিয়াম গিফ্ট’, Ôগুজবের হাত-পা’, Ôআরেক রফিক আরেক সালাম’, Ôদেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন
জুয়া এ’ এবং ‘‘বাংলা একাডেমীর বইমেলা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা’। এমন-কি,
তার উচাটন ভাবনা থেকে বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যা ও
পানিব্যবস্থাপনার মতো বিষয়টিও বাদ পড়ে নি। বলা যেতে পারে, ছফা মানসে এইসমূহ বিষয়াদি এক
প্রকারের জটিলতা তৈরি করে রেখেছিলো। কেউ কেউ ছফার এই বিষয়সমূহের প্রতি তিব্র প্রতিক্রিয়াকে এক ধরনের বিকার বলে দাবী করলেও তাঁর সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি সচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অর্থেই তা
সত্য হতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে এইসমূহ ব্যাপারের মধ্যেই অবক্ষয়রূপ বিকার বাসা বেঁধেছিলো আর তা-সব ছফা তাঁর সৎ ও স্বচ্ছ¡ মানসে প্রায়শ মানতে পারতেন না,
ফলে প্রতিক্রিয়া দেখাতেন এবং লোকমুখে তিনি ঠোঁটকাটা বা উচিত বক্তা হিসেবেও খ্যাতি কিংবা অপখ্যাতি পেয়েছিলেন।
কয়েকটি লেখার শিরোনাম থেকেই বোঝা গেছে তাঁর প্রতিক্রিয়ার অন্যতম একটি স্থান হলো ভারতের পশ্চিম বাংলার মানুষ, সাহিত্য, সাহিত্যিক, সাহিত্যিক প্রয়াশের আড়ালের শঠতা, প্রকাশককুল ও পত্র-পত্রিকারসমূহ। Ôআনন্দবাজার উপাখ্যান’ প্রবন্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়ার চরম প্রকাশ ঘটেছে।
আনন্দবাজার পত্রিকার কিংবদন্তীতুল মিথ্যেবাদিতার সত্যটি প্রকাশে তাঁকে পৌরাণিক উপকথার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, এখানে প্রচ্ছন্নে হীনমন্যতার অভিব্যক্তি নিশ্চয় ছিলো।
অবশ্য হীনমন্যতা যে কেবল এক পাক্ষিক তা নয়, বরং তা
দ্বিপাক্ষিক। তবু, এই হীনমন্যতা দ্বিপাক্ষিক হলেও এর
স্বরূপ কিন্তু আলাদা এবং স্বতন্ত্রই। তবে, হীনমন্যতার পিছনের কারণসমূহের মধ্যে সাধারণ যে বিষয়টি ছিলো এবং এখনও আছে, তা হলো দুই বাংলার মানুষের ভাষা ও সাংস্কৃতিক পূর্বসূত্র, যা কখনোই কোনো পক্ষই ভুলে যেতে পারে না। হীনমন্যতার পশ্চাতে থাকে বিকাশসম্ভাবী অহংকারও। অহংকার হলো স্বতন্ত্রতার, স্বয়ং স্বীয় শক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায়। এই প্রচেষ্টার মধ্যে সাহিত্য-সাংস্কৃতির ক্ষেত্রটি অন্যতম প্রধান।
সে পর্যন্ত সাধারণ স্বীকার্য, এবং অনস্বীকার্য ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিলো যে
পশ্চিম বাংলার সাহিত্য অপেক্ষকৃত শ্রেতর, বাংলাদেশের সাহিত্যের তুলনায়, যদিও উভয়ই বাংলাভাষার সাহিত্য। ভাষার ঐক্য এখানে সবসময়ে একটি অন্তরের আত্মীয়তার বৈজয়ন্তীকে উড্ডীন রাখলেও বাংলাদেশের স্বতন্ত্র হওয়ার ও
আপন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রচেষ্টার ভিতরে বারে বারেই পশ্চিমবাংলার শ্রেয়তা এসে ঢুকে পড়তে চেয়েছে।
আর এখানে বাংলাদেশের লেখককুলের হীনতা এই
যে, তারা আত্মকৃত শ্রেয়তা অর্জনের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গীয় শ্রেয়তার নিকট বারে বারেই তার আনুগত্য নিয়ে গেছে আর
মামুলি স্বীকৃতি কিংবা সামান্য শংসাবাণী শুনতে ধর্না দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার লেখক ও
প্রকাশক গোষ্ঠী বাংলাদেশকে চেয়েছে সর্বদাই তাদের সাহিত্যের বাজার হিসেবে। Ôপশ্চিমবাংলার বই বাংলাদেশে কাদের স্বার্থে’ শিরোনাম রচনাটিতে ছফা এই
বাজারবাস্তবতাটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। ÔভাবুকমÐলী,
আনন্দোগোষ্ঠী এবং আরো কিছু প্রসঙ্গ’ শিরোনাম লেখাটিতে স্পষ্ট হয় পশ্চিমবাংলার লেখককুল বাংলাদেশের সাহিত্যের মূল্যায়ন কীদৃষ্টিতে করেন। তারা বাংলাদেশকে হেয় করার নানান ফাঁদ পেতে রাখে আর বাংলাদেশের উচ্ছিষ্টভোগী লেখককুল সেই টোপ গিলে থাকে।
এবং তাদের এই
প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়াসমূহ বাংলাদেশের আত্মমর্যাদাশীল হয়ে দাঁড়ানোর পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।
তিনি Ôদেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন যুয়া এ’ প্রবন্ধে দেশিয় লেখককুলের প্রতি কটাক্ষ করেন এবং সাহিত্যের বিকাশে বাংলাদেশের সাহিত্যিকগোষ্ঠীর ব্যর্থতা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি সুষ্পষ্ট দেখিয়ে দেন।
দেশ পত্রিকা ও
কলকাতার সাহিত্য বাংলাদেশে দেশিয় সাহিত্যের ক্ষতির খতিয়ান দেন তিনি আর
ভর্ৎসনা করেন দেশিয় সাহিত্যিককুলে যারা তা
অনুধাবনে ব্যর্থ। এইসমূহ কথা ও
উচ্চবাচ্যের পরেও পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক দখলদারিত্বের প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত আর তারা কিছু সফলও হয়েছে বলতে হবে। এবং এটা স্পষ্টতই বাংলাদেশের প্রতি ভারতের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিরও অংশ। সমভাষার দাবীদে যে
লেনদেন চলছিলো তা
মূলত একমুখী থেকেছে।
তাই বারে বারেই ছফার তীব্র প্রতিক্রিয়া আনন্দবাজারের কর্মকাÐে,
দেশ পত্রিকার প্রবেশে ও
পশ্চিবাংলার বইমেলার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায়। আনন্দ বাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে যদিও দুই বাংলার লেখক সম্প্রদায়ের অনেকেরই অভিযোগসাম্য রয়েছে কিছু বিষয়ে, তা হলো এর পুঁজিবাদী স্বার্থ, লেখকদের শোষণ-শাসন, লেখকের লেখকত্ব গ্রাস করার নানান ফাঁদ। কিন্তু, তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রতি দেশ পত্রিকার বিরূপ সাংস্কৃতিক এজেন্ডাসমূহ কখনো গোপন থাকে নি। আর নানান রাজনৈতিক সমীকরণের মুখে বাংলাদেশের রাজনীতিকগণের নতজানু অবস্থানও জাতিসত্তাকে লজ্জায় ফেলেছে বার বার। Ôকলকাতা বইমেলা: একটি বিশ্লেষণ’ শিরোনাম লেখাটিতে ছফা বাংলাদেশের প্রতি পশ্চিমবাংলার দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট করেছেন এবং তাদের প্রতি বাংলাদেশের নতজানু অবস্থান ও অন্তরের গোপন আনুগত্যটিও প্রতিভাসিত হয়েছে। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমীকরণে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ প্রায়শ উপেক্ষিত হয়েছে এবং এখনো তা
অব্যাহত। এখানে সম্পর্কের অবমাননাজাত প্রশ্নটি এই যে, ১৯৪৭ পূর্ববর্তী ভারতীয় রাজনীতির যে স্বর্ণস্বপ্ন ছিলো ভারতবর্ষের সকল জাতির সমন্বয়ে একজাতি Ôভারতীয় জাতি’ গঠনের, সেই স্বপ্নের অংশ কি এই, বাংলাদেশের প্রতি তাদের এই আচরণ? রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এই প্রশ্নটিকে কিছুতেই অমূলক প্রমাণ করতে পারে না।
পূর্বেই বলেছি, পশ্চিমবাংলার হীনমন্যতার স্বরূপটি কিছু ভিন্ন।
তাদের হীনমন্যতার বীজটি রয়েছে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের কুখ্যাত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অপচেষ্টার মধ্যে এবং অবশেষে ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ হয়ে যাওয়ার মধ্যে। তাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে ভাষা-সম্পর্কের ও সাংস্কৃতিক বিভাজনের এবং ঘটেছে মানুষের স্থানিক বিচ্যুতি ও হতে হয়েছে বিশাল সংখ্যক মানুষের ভূমি থেকে উন্মূল।
ভারত বিভাজনের অন্যতম প্রধান নায়ক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ চেয়েছিলেন, ব্রিটিশদের প্রস্থানপরবর্তী ভারতের রাজ্যসমূহ পাক তাদের স্বতন্ত্রতা এবং তাদের রাজ্যের স্বতন্ত্রতাকে প্রধান রেখেই যেন তারা কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।
কিন্তু ভারতের কেন্দ্র শাসন বরাবরই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যচেতনাকে অবদন করতে চেয়েছে। পশ্চিমবাংলার ভাষা-সংস্কৃতিও সেই অবদমনের শিকার হয়েছে নির্মমভাবে। পক্ষান্তরে অপর বাংলা তথা বাংলাদেশ স্বাতন্ত্রে দাঁড়াতে চেয়েছে এবং দাঁড়িয়েছে অহংকারে মাথা তুলে। এই অহংকারই পশ্চিমবাংলাকে হীনমন করে তোলে। পশ্চিমবাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশসমূহ যে অবদমনের শিকার হয়েছে ও হচ্ছে তার অন্তরালে ও কেন্দ্রে রয়েছে ভারতের রাজনীতির বদখত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবতা। সেটি হলো ভারতের একজাতি তত্ত¡। ভারত স্বাধীন হবার পূর্বমুহূর্তে সেই তত্ত্বের উৎপত্তি। এবং দ্বিধাহীন বলা যেতে পারে যে, এই ঐক্যকামী তত্ত্বটি ছিলো নিতান্তই মেকি ও বাস্তবতা বিবর্জিত। ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিছুতেই এই তত্ত্বের অনুকূল ছিলো না। ফলত, এটা বলা যেতেই পারে যে সৈয়দ আহমদ প্রবর্তিত দ্বিজাতি তত্ত্বটি মূলত এবং প্রকৃত অর্থেই ভারতের (বলা ভালো কংগ্রেসের) একজাতি তত্ত্বেরই বিপরীত প্রতিক্রিয়াপ্রসূত এবং বাস্তবে প্রতিফলিত। এই রাজনৈতিক বাস্তবতায় কালক্রমে পশ্চিমবাংলার মানুষের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে সংকটে পড়েছে, সংকট পোহাচ্ছে; সেই বাস্তব পরিস্থিতির অনুধাবনজাত হীনমন্যতাবোধ তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বহুদিন ধরে এবং বাংলাদেশের সাথে তাদের শিল্প-সাহিত্য ও
সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়াপ্রচেষ্টার অনেকখানিই সেই হীনমন্যতাজাত। কিন্তু, এর মধ্য থেকেই বাংলাদেশের প্রতি তাদের তাচ্ছিল্যের ভাবটিও তারা গোপন রাখে না। স্বদেশ ও স্বজাতিকে নিয়ে ভীষণরূপে শ্লাঘাবোধ করা ছফার কাছে এই তাচ্ছিল্যটুকু মেনে নেয়া সহজ নয় মোটেই। ফলে, তিনি প্রতিবাদে কলকলিয়ে ওঠেন।
এতো গেলো বাহির দিকের উপদ্রব। কিন্তু, অভ্যন্তরের আরো আরো পচনগুলোও কি কম পীড়ার! পচনক্রিয়া! পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই সব ক্ষয়ে শেষ হবার উপক্রম এখানে।
পৌরাণিক রচিত্র যযাতির উদাহরণ তুলে এনে ছফা দেশের প্রবীণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর মানসবিকৃতির স্বরূপটি উন্মোচন করেন তার ‘যযাতির গল্প’ শিরোনাম লেখায়। বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির অবক্ষয়িতরূপ কতোটা বিকৃত তা ধরা পড়ে ২০০০ সালের নিউইয়ার উদযাপনের কালে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের টিএসসি’র ঘটনাটি থেকে।
সাংস্কৃতিক মানের বিচারে বৈশ্বি^ক এমডিজি প্রকল্প যে
বাংলাদেশে অশ^ডিম্বই প্রসব করেছে তা বলাই যায়।
পরবর্তী আরো আরো ঘটনার মধ্যদিয়ে সেই বিকৃতি দন্তবিকশিত করেছে। আমরা তার নিঃসহায় দর্শক। এই হলো বাংলাদেশের জন্য উন্নয়নের নামাঙ্কিত Ôমিলেনিয়াম গিফ্ট’। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দেওলিয়াত্বও আড়াল থাকে নি। Ôগুজবের হাত-পা’ বাংলাদেমের রাজনৈতিক বিকৃতির বিষয়ে একটি স্মারক রচনা।
ছফা বারে বারেই এই বিকৃতির ব্যাপারে সখেদ প্রতিক্রিয়া বাঙ্ময়। রাজনীতি যে কতোটা আত্মঘাতী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলা একাডেমির বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও পক্ষপাতমূলক রাজনৈতিক অবস্থান। বাংলাদেশের রাজনীতির আরেক লাম্পট্যরূপক স্বরূপ দেখি একুশে ফেব্রæয়ারি’র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পেছনের কৃতিত্ব দাবি নিয়ে। একুশ আমাদের অবিসংবাদিত গৌরবের চিহ্ন। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য আত্মদানকারি রফিক, সালাম, জাব্বার, বরকত প্রমুখের নাম কে না জানেন। কিন্তু একুশে ফেব্রæয়ারি দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠার পিছনে যে
আরেক রফিক, আরেক সালামের ভিত্তিগত অবদান তা
সকলেই বেমালুম ভুলে গেলো কিংবা অস্বীকার করলো। অস্বীকারই করেছে বলতে চাই, কেন না,
রাজনৈতিক একটি পক্ষ এই অস্বীকৃতির মধ্যদিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দাবি করে তা
তাদের রাজনৈতিক সাফল্য, এই বলে প্রচারে মুখর হয়েছে। এই বিকারসমূহ কি বাংলাদেশের সংকটকালকে চিহ্নিত করে না? নিশ্চয়ই করে।
এবং এই বিকারসমূহ পর্যবেক্ষণে ছফা তাঁর সচেতনমানসে শঙ্কা ও
সংশয়ে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, উচাটন বোধ করেছেন দেশ, মানুষ ও জাতিসত্তার ভবিষ্যতের দুর্ভোগ চিন্তা ও
বেদনায়।
লেখক পরিচিতি:
 |
| শামীম সাঈদ ( জন্ম: ১৯৭৯) |
শামীম সাঈদ কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। জন্মকাল ১০ জানুয়ারি, ১৯৭৯ সাল।
জন্মস্থান কলসনগর, লালপুর, নাটোর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বে
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। শিল্পসাহিত্যের ত্রৈমাসিক ‘অনুপ্রাণন’ এর সদস্য
সম্পাদক।
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: এই কথা বৃষ্টিবাচক (২০১৩), এভাবে
খুলবে না আঁচলের খুঁট (২০১৪), সদা ভাগতেছে ভববান (২০১৪), নাঙ পূরাণ (২০১৭) ও
স্বৈরমতি পিরিতের শূল (২০১৮)। সম্পাদিত গল্পগ্রন্থ: কুঁড়িকাল ও যুগযাপনের গল্প (২০১৪)।









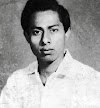





0 মন্তব্যসমূহ